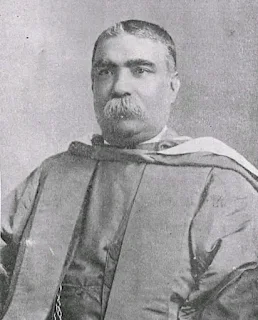* নদীয়ার সন্দেশ
বরিশালের ব্র্যান্ড
-----
.
ঘটনাটি ষাটের দশকের। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ায় আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে গিয়ে প্রথম পরিচয় হয়েছিল সাদা ধবধবে এক ধরনের মিষ্টির সঙ্গে। কিছুটা নরম, আকৃতিগত দিক থেকে এবড়ো-থেবড়ো। সেই মিষ্টিতে মন ভরেছিল সতীশ চন্দ্র দাসের। বরিশালের উজিরপুর উপজেলার গুঠিয়া গ্রামের নিজ এলাকায় ফিরে এসে তৈরি করলেন নদীয়ার সেই সন্দেশ। সঙ্গে স্হানীয় উপকরণ ও পদ্ধতি ব্যবহার করা হলো। নামকরণ করা হয় গুঠিয়ার সন্দেশ।
দূর থেকে দেখতে শিউলি ফুলের মতো। নতুন এই সন্দেশ বাজারজাতকরণে তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন ব্যবসায়ী বন্ধু বাদশা হাওলাদারকে। ১৯৬২ সালে তারা দুজনে নতুনভাবে উৎপন্ন সন্দেশ বিক্রি করে সাড়া ফেলে দেন। সতীশ ও বাদশা দুজনের কেউই এখন আর বেঁচে নেই। কিন্তু তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ গুঠিয়ার সন্দেশ বরিশাল অঞ্চলে বিখ্যাত। রীতিমতো বরিশালের ব্র্যান্ড। গুঠিয়ার গ্রাম্য হাটের জৌলুস কমেছে, পাশের বিশাল খালটি তার নাব্য হারিয়েছে। কিন্তু সন্দেশের বাজার আজও জমজমাট। প্রতিদিন দেশ ও দেশের বাইরের ভোজনরসিকরা এই মিষ্টান্নের স্বাদ পেতে ছুটে আসেন গুঠিয়ায়। ব্যবসায়ীরা বলছেন, আন্তর্জাতিক বাজার পেলে সেখানেও বাজিমাত করবে গুঠিয়ার সন্দেশ।
বাঙালির খাদ্যপণ্যের তালিকায় সন্দেশ নতুন নয়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং চৈতন্যের কবিতায় সন্দেশের উল্লেখ রয়েছে।
সন্দেশ সাধারণত নরম ও লঘুপাকের হয়। কিন্তু গুঠিয়ার সন্দেশ ঠিক তার উল্টো, কড়াপাকের। এজন্য গুঠিয়ার সন্দেশ হয় কিছুটা শক্ত ও শুষ্ক। অন্যসব জায়গায় ক্ষীর সন্দেশ, সরপুরি, সাদা সন্দেশ, গুড়ের সন্দেশ, পোড়া সন্দেশের মতো হরেক নামে সন্দেশ পেলেও গুঠিয়ার সন্দেশ প্রধানত এক পল্লার ও দুই পল্লার। দুই পল্লার সন্দেশকে ডাকা হয় জোড়া সন্দেশ নামে।
গুঠিয়া বাজারে এখন মাত্র সাতটি সন্দেশের দোকান চালু রয়েছে। এরমধ্যে মাহিয়া মিষ্টান্ন ভান্ডারের স্বত্বাধিকারী টিটুল হাওলাদার জানান, প্রতিদিন যত মানুষ এই বাজারে মিষ্টান্ন নিতে আসেন তার আশি ভাগই সন্দেশ নিতে আসেন। সন্দেশ শুধু নিজে খান এমন না, স্বজনদের জন্যও নিয়ে যান। দেশের বাইরেও অনেকে নিয়ে যান।
এই দোকানের কর্মচারী মিন্টু হাওলাদার বলেন, গুঠিয়ার সন্দেশ তৈরিতে কোনো ধরনের ভেজাল দ্রব্য দেওয়ার সুযোগ নেই। আমরা গুণগত মান ঠিক রেখেই সন্দেশ বিক্রি করি। তিনি আরও বলেন, গুঠিয়ার সন্দেশের চাহিদা দেশ ও দেশের বাইরে অনেক। কিন্তু দুধ ও চিনির দাম যেভাবে বাড়ছে তাতে আর আগের দামে সন্দেশ বিক্রি করতে পারছি না। তার ওপর আয়কর অফিস আমাদের ওপর বিনা কারণেই বাড়তি কর ধার্য করছে।
আরেক কারিগর শ্যামল চন্দ্র বলেন, আমার পূর্বপুরুষ ছিলেন সতীশ চন্দ্র দাস। তিনি যে পদ্ধতিতে সন্দেশ তৈরি করতেন আমরা এখনো সেভাবেই তৈরি করে থাকি। এজন্যই গুঠিয়ার সন্দেশের সঙ্গে দেশের আর কোনো জায়গার সন্দেশ মিলবে না। আমরা খাঁটি দুধ ও চিনি ব্যবহার করি। তিনি আরও বলেন, খাঁটি পণ্য বিক্রি করায় সম্প্রতি ঢাকার চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে সরকার আমাকে পুরস্কৃত করেছেন। সরকার আশ্বস্ত করেছে ঐতিহ্যবাহী খাদ্যপণ্য হিসেবে এই সন্দেশ তারা আন্তর্জাতিকভাবে বাজারজাত করবে। সেই সুযোগ পেলে গুঠিয়ার সন্দেশ নিঃসন্দেহে বিশ্ব বাজারও জয় করবে। বর্তমানে প্রতি কেজি সন্দেশ সাতশ টাকা বিক্রি হচ্ছে।
এই সন্দেশ সুস্বাদু ও মানসম্পন্ন হওয়ায় এর চাহিদা বেশি। তবে এর উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা না থাকায় সবাই এই মিষ্টি প্রস্তুত করতে পারেন না। প্রতিদিন ৫০০ কেজির বেশি চাহিদা থাকলেও উৎপাদন অর্ধেকের চেয়েও কম।